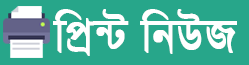
সম্পাদকীয়
বর্তমান বিশ্বে গণতান্ত্রিক নির্বাচনব্যবস্থার বৈচিত্র্য ও বিকল্প ব্যবস্থাগুলোর মধ্যে অন্যতম আলোচিত একটি পদ্ধতি হচ্ছে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বমূলক (Proportional Representation – PR) পদ্ধতি। বাংলাদেশে সাম্প্রতিক সময়ে রাজনৈতিক অঙ্গনে পি আর পদ্ধতির প্রবর্তন ও চর্চার দাবি নতুন করে উচ্চারিত হচ্ছে। এই দাবি শুধু নির্বাচন প্রক্রিয়ার পরিবর্তন নয়, বরং একটি বৃহত্তর রাজনৈতিক সংস্কৃতির রূপান্তরের ইঙ্গিত বহন করে।
পি আর পদ্ধতি: একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয়
পি আর পদ্ধতির মূল ভাবনা হলো— জনগণের ভোটের অনুপাতে রাজনৈতিক দলসমূহকে আসন বরাদ্দ দেয়া। এতে প্রত্যেক ভোটের একটি মূল্য থাকে এবং ছোট দলগুলোও প্রতিনিধিত্ব পাওয়ার সুযোগ পায়। বর্তমান বাংলাদেশে প্রচলিত “ফার্স্ট পাস্ট দ্য পোস্ট” (FPTP) পদ্ধতিতে শুধুমাত্র যে প্রার্থী সবচেয়ে বেশি ভোট পান, তিনিই নির্বাচিত হন— যদিও সেটা মোট ভোটের মাত্র ৩০-৩৫% হতে পারে। এতে বাকি ৬৫-৭০% ভোট কার্যত বিফলে যায়।
রাজনৈতিক দলগুলোর দাবি
বর্তমানে কয়েকটি রাজনৈতিক দল, বিশেষত ছোট এবং বিকেন্দ্রীকৃত দলগুলো, পি আর পদ্ধতির জন্য সোচ্চার। তাদের যুক্তি হল— বর্তমানে বিদ্যমান একক-প্রার্থীভিত্তিক নির্বাচনী ব্যবস্থায় বড় দলগুলো ক্ষমতার দখল নিশ্চিত করে, কিন্তু ভোটারের আসল রায় প্রতিফলিত হয় না।
পি আর পদ্ধতির মাধ্যমে তারা প্রতিনিধিত্বে ন্যায্যতা, সংসদে বহুত্ববাদ, এবং রাজনৈতিক বিকেন্দ্রীকরণের আশা করছে। বিশেষ করে তৃণমূল বা স্থানীয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণকারী দলগুলোর জন্য এটি বড় সম্ভাবনার দ্বার খুলে দেয়।
সমালোচনা ও শঙ্কা
অবশ্য এই পদ্ধতির বিরুদ্ধেও বেশ কিছু সমালোচনা রয়েছে। যেমন—
১. সরকার গঠনে জটিলতা: একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়া কঠিন হওয়ায় জোট সরকার গঠনের প্রয়োজন হয়, যা অস্থিতিশীলতা ডেকে আনতে পারে।
২. দলভিত্তিক ভোট: অনেক ক্ষেত্রেই জনগণ প্রার্থীর যোগ্যতার চেয়ে দলে ভোট দেন, ফলে ব্যক্তিকেন্দ্রিক জনপ্রিয়তা মূল্যহীন হয়ে পড়ে।
৩. চিন্তাহীন জোট: নানা মত ও নীতির দল জোটে গিয়ে নীতির শিথিলতা তৈরি করতে পারে।
বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে প্রাসঙ্গিকতা
বাংলাদেশের মতো দেশে, যেখানে দুইটি প্রধান দল প্রায় একচেটিয়া রাজনীতি চালায়, পি আর পদ্ধতির বাস্তবায়ন একটি নতুন রাজনীতির সম্ভাবনা সৃষ্টি করতে পারে। এর ফলে অনেক দীর্ঘদিন ধরে প্রান্তিক ও নবীন রাজনৈতিক শক্তিগুলো জাতীয় রাজনীতিতে প্রবেশাধিকার পেতে পারে।
এছাড়া পি আর পদ্ধতি সংবিধান সংশোধন, নির্বাচন কমিশনের কাঠামোগত সংস্কার, এবং ব্যাপক রাজনৈতিক ঐকমত্য ছাড়া সম্ভব নয়। এটি শুধু একটি প্রযুক্তিগত পদ্ধতি নয়; বরং একটি রাজনৈতিক সংস্কৃতির প্রতিফলন, যেখানে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, সহাবস্থান এবং বহুত্ববাদকে গুরুত্ব দেয়া হয়।
পরিশেষে:
বাংলাদেশের নির্বাচনী ব্যবস্থায় জনগণের প্রকৃত মতামতের প্রতিফলন, রাজনৈতিক অন্তর্ভুক্তি এবং গণতন্ত্রের বিকাশে পি আর পদ্ধতি একটি কার্যকর বিকল্প হতে পারে। তবে এর জন্য চাই রাজনৈতিক সদিচ্ছা, গভীর গণতান্ত্রিক চেতনা এবং একটি কার্যকর আলোচনার পরিবেশ।
এই পদ্ধতি শুধু ক্ষমতার ভাগাভাগি নয়, বরং একটি বিকল্প রাজনৈতিক দর্শনের দিকে অগ্রসর হওয়া, যেখানে প্রতিটি ভোটই মূল্যবান, এবং প্রতিটি কণ্ঠস্বরই প্রতিনিধিত্বযোগ্য।