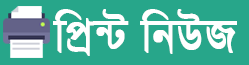
নিউজ ডেস্ক, জনতারকথা।
গেল কয়েক মাস ধরে নির্বাচনে পিআর বা আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব নিয়ে এত আলোচনা-বিতর্ক চলমান যে, গ্রামের চায়ের দোকানে আড্ডা দেওয়া ব্যক্তিটিও এখন কারোর চেয়ে কম জানেন না। এ নিয়ে গণমাধ্যমে প্রকাশিত সবশেষ প্রতিবেদনগুলোর দিকে দৃষ্টি দিলে সহজেই এর ব্যাপকতা আঁচ করা যাবে।
রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও বিশ্লেষকদের ভাষ্যে, আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন পিআর পদ্ধতিতে করার দাবিকে ঘিরে বিরাজমান উত্তেজনা সামনের দিনে নি:সন্দেহে প্রকট হতে চলেছে। পিআর পদ্ধতি নিয়ে রাজনৈতিক উত্তেজনার মাঝেই আরও একবার এই পদ্ধতির আদ্যোপান্ত জেনে নেব আমরা।
বাংলাদেশে প্রচলিত নির্বাচন পদ্ধতিতে অনেক সময় ভোটের পরিসংখ্যান এবং সংসদীয় আসনের মধ্যে বড় ধরনের অসামঞ্জস্য দেখা যায়। সামান্য কিছু বেশি ভোট পেয়ে কোনো দল বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে, আবার কাছাকাছি ভোট পেয়েও অন্য দল পায় নামমাত্র আসন। এর কার্যকর বিকল্প হিসেবেই উঠে আসে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব বা প্রপোরশনাল রিপ্রেজেন্টেশন (পিআর) পদ্ধতি। বিগত ৫ আগস্ট ২০২৪ শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর এই পিআর পদ্ধতির দাবি উঠতে থাকে রাজনৈতিক মহল থেকে।
পিআর পদ্ধতি বা আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব এমন একটি নির্বাচন ব্যবস্থা যেখানে প্রতিটি রাজনৈতিক দল বা জোট প্রাপ্ত ভোটের হারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বা আনুপাতিক হারে আইনসভায় আসন লাভ করে। যার স্পষ্ট অর্থ হচ্ছে-কোনো দল যদি নির্বাচনে মোট ভোটের ২০% পায়, তবে আইনসভার মোট আসনের প্রায় ২০% তাদের প্রাপ্য হবে। ভোটারদের রায় প্রতিফলিত হওয়ার সঙ্গে এই পদ্ধতির মূল উদ্দেশ্য, ভোটের অপচয় রোধ করে সংসদে সব মতের মানুষের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা।
দৃষ্টান্ত স্বরূপ, ২০০১ সালের জাতীয় নির্বাচনে বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোট ৪০.৮৬% ভোট পেয়ে ১৯৩টি আসন লাভ করলেও প্রায় সমান ভোট (৪০.২২%) পেয়েও আওয়ামী লীগ জয়ী হয় মাত্র ৬২টি আসনে। তারমানে বর্তমানে প্রচলিত পদ্ধতিতে প্রাপ্ত ভোট ও আসনের মধ্যে কোনো আনুপাতিক সামঞ্জস্য নেই। পিআর পদ্ধতির স্বপক্ষে থাকা রাজনৈতিক দলগুলো বলছে, পিআর পদ্ধতি নিয়ে চালু থাকলে ভোটের এই বিশাল ব্যবধান দূর করে সংসদ আরও প্রতিনিধিত্বমূলক হতো।
নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে সংলাপে বেশ কিছু রাজনৈতিক দল পিআর পদ্ধতির পক্ষে মতামত জানিয়ে বলেছেন, এর মাধ্যমে ছোট দলগুলোরও সংসদে আসার সুযোগ তৈরি হবে এবং ভারসাম্যপূর্ণ রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে উঠবে।
আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব বা পিআর পদ্ধতি কেবল একটি বিকল্প নির্বাচন ব্যবস্থা নয়, এটি গণতন্ত্রকে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক, ন্যায্য এবং কার্যকর করার একটি শক্তিশালী মাধ্যম। এর মাধ্যমে আইনসভায় জনগণের প্রকৃত ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটে, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বাড়ে এবং উগ্রপন্থা হ্রাস পায়। উন্নত বিশ্বের অভিজ্ঞতা এবং বাংলাদেশের বিগত নির্বাচনগুলোর ফলাফল বিশ্লেষণ করলে স্পষ্ট হয় যে, দেশের গণতান্ত্রিক যাত্রাকে আরও অর্থবহ করতে পিআর পদ্ধতি নিয়ে নতুন করে ভাবনার সময় এসেছে।
তবে বিশ্লেষকরা বলছেন, মূলনীতিতে এক হলেও একেক দেশের ‘পিআর’ একেক রকম। একটির সঙ্গে অন্যটির তেমন মিল নেই। এই পদ্ধতিতে নির্বাচন ব্যক্তি-প্রার্থীদের মধ্যে হয় না। নির্বাচন হয় রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে। খুব সহজভাবে বলতে গেলে, এই পদ্ধতির নির্বাচনে যে দল মোট প্রদত্ত ভোটের মধ্যে যত শতাংশ ভোট পাবে, সেই অনুপাতে সংসদেও তত ভাগ আসন পাবে। যেমন—বাংলাদেশের ৩০০ আসনের সংসদে ১ শতাংশ ভোট পাওয়া দল ৩টি আসন পাবে। ১০ শতাংশ ভোট পেলে আসন পাবে ৩০টি।
ভালো-মন্দ
নির্বাচন বিশ্লেষক ও স্থানীয় সরকার বিশেষজ্ঞ তোফায়েল আহমেদ গণমাধ্যমকে বলছেন, ‘রাজনৈতিক দলগুলোর কোনো রিফর্ম না করে পিআর পদ্ধতি চালু করেও সহজে এখান থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে না। কারণ, পিআর করলে তাদের সুবিধাটা বেড়ে যাবে। কারণ লোকে তো পার্টিকে ভোট দেবে। তখন পার্টি তার ইচ্ছেমতো প্রার্থী দিয়ে দিতে পারবে। তখন সেটা তাদের জন্য আরও সুবিধার হয়ে যাবে।’
তবে এই পদ্ধতির ইতিবাচক দিক সম্পর্কে তিনি, ‘এই পদ্ধতিতে এক দলের মনোপলি হবে না। ধরা যাক, পিআর পদ্ধতিতে ১ শতাংশ ভোট যারা পাবে, তাদের থেকে শুরু হবে আসন বণ্টন। এতে সব দল হয়তো কোনো না কোনো আসন পাবে।’
পিআর পদ্ধতির আরেকটি অসুবিধার দিক নিয়ে এই বিশ্লেষক বলছেন, ‘এই পদ্ধতিতে দলগুলোর ইচ্ছাকৃতভাবে স্বামী-স্ত্রী-আত্মীয়স্বজনকে মনোনয়ন দেওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। কারণ ভোটার তো পার্টিকে ভোট দেবে। ব্যক্তিকে ভোট দেবে না। আগে তালিকা দিলেও মানুষের চয়েসটা এখানে থাকবে না।’
তবে সীমিত পরিসরে এ নীরিক্ষাটা করা যেতে পারে মন্তব্য করে তোফায়েল আহমেদ বলেন, ‘নেপালে বেশ জটিল একটা পদ্ধতি আছে। আমাদের দেশের মানুষের জন্য বোঝা একটু কঠিন হবে। তাই উচ্চকক্ষের অর্ধেক আসনের জন্য এই পদ্ধতি কার্যকর করা যেতে পারে কিনা সেটা ভাবা যেতে পারে। যেহেতু বিষয়টা নিয়ে আলাপ উঠেছে এবং কিছু লোক এটাকে সাপোর্ট করছে।’
পিআর পদ্ধতিতে রাজনৈতিক দল যে ক্রমতালিকা করবে, তাতে কোনো বাণিজ্য হবে না– তা কীভাবে নিশ্চিত করা হবে-এমন প্রশ্ন তুলে বিশ্লেষক আ ক ম সাইফুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, ‘কোনো প্রার্থী মনোনয়ন বাণিজ্য করে মনোনয়ন কিনলে তাতে ভোটারের কোনো উনিশ-বিশ হয় না। মনোনয়ন বাণিজ্যে হেরে যাওয়া ব্যক্তিও নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়ে বিজয়ী হওয়ার প্রচুর উদাহরণ আছে। অথচ পিআর পদ্ধতিতে কোনো ব্যক্তি রাজনৈতিক দলের অনুগ্রহ ছাড়া সংসদ সদস্য হতে পারবেন না।’
রাজনৈতিক বিশ্লেষক মহিউদ্দিন আহমদের মতে, যে বড় দলগুলো মনে করে যে তারা নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে পারে, তারাই এটার বিরোধিতা করছে। কারণ এখানে তারা কোনো শেয়ারহোল্ডার চায় না।‘
তিনি বলেন, ‘এমনও হতে পারে যে নিম্মকক্ষের ৩০০ আসনে সরাসরি ভোট হলো। আর সংরক্ষিত নারী আসনের মধ্যে ৫০টির ভোট পিআর পদ্ধতিতে হলো। সেইসঙ্গে উচ্চকক্ষের সবগুলো আসনের ভোটও পিআর পদ্ধতিতে হতে পারে। অর্থাৎ সরাসরি ভোট এবং পিআর পদ্ধতি—দুটোর সংমিশ্রনেই একটা ব্যবস্থা করা যায়।’
পুরো বিষয়টি রাজনৈতিক সদিচ্ছার ওপর নির্ভর করবে উল্লেখ করে রাজনৈতিক বিশ্লেষক বিভুরঞ্জন সরকার বলেন, ‘বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ গণতন্ত্রে আমরা যদি আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক, বৈচিত্র্যময় ও জবাবদিহিমূলক সংসদ চাই, তাহলে পিআর পদ্ধতির কথা আরও গুরুত্ব দিয়ে ভাবতে হবে। এটা নিছক একটি নির্বাচন পদ্ধতির প্রশ্ন নয়, এটা একটি রাষ্ট্রের রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও গণতান্ত্রিক চরিত্র গঠনের প্রশ্ন।’
‘যদি প্রস্তুতি না থাকে, তাহলে এই পদ্ধতি ব্যর্থ হবে এবং আরও বিভ্রান্তি তৈরি করবে। কিন্তু যদি রাজনৈতিক সদিচ্ছা, আইনগত কাঠামো ও সামাজিক প্রস্তুতি থাকে, তাহলে এটি হতে পারে আমাদের গণতান্ত্রিক অভিযাত্রার এক নতুন ও ইতিবাচক অধ্যায়’-বলেন এই বিশ্লেষক।
পেছনের ইতিহাস
আধুনিক বিশ্বে সর্বপ্রথম ১৮৯৯ সালে বেলজিয়ামে পিআর পদ্ধতির মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। জার্মানি, সুইডেন, সুইজারল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, স্পেন এবং লাতিন আমেরিকার প্রায় সব দেশেই এই ব্যবস্থা প্রচলিত। বর্তমানে বিশ্বের ১৭০টি গণতান্ত্রিক দেশের মধ্যে ৯১টি দেশ, অর্থাৎ প্রায় ৫৪% রাষ্ট্র, তাদের আইনসভা নির্বাচনে কোনো না কোনো ধরনের পিআর পদ্ধতি ব্যবহার করে। অর্থনৈতিকভাবে উন্নত দেশগুলোর সংগঠন ওইসিডি (OECD)-এর ৩৬টি সদস্য দেশের মধ্যে ২৫টি, অর্থাৎ প্রায় ৭০% দেশ, এই পদ্ধতি অনুসরণ করে।
ইউরোপের নেদারল্যান্ডস, সুইডেন, ফিনল্যান্ড, বেলজিয়াম, জার্মানি (আংশিক); এশিয়ায় ইসরায়েল, ইন্দোনেশিয়া ও নেপাল; আফ্রিকায় দক্ষিণ আফ্রিকা ও নামিবিয়া; লাতিন আমেরিকায় ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনা এবং উত্তর আমেরিকায় আংশিকভাবে কানাডার পিআর পদ্ধতিই আলোচনার দাবি রাখে। তবে বিশ্বে পিআর পদ্ধতির একটি ক্লাসিক উদাহরণ হচ্ছে ইসরায়েল, যেখানে পুরো দেশই একক ভোট এলাকা। যে দল মাত্র ৩.২৫ শতাংশ ভোট পায়, তারাও আসন পায়। এতে ছোট দলগুলো সব সময় সংসদে প্রবেশ করে।
তবে এ পদ্ধতির কারণে দেশটির সরকার নানা ধরনের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় জটিলতার মুখে রয়েছে। বিশ্লেষকদের মতে, পিআর পদ্ধতি মোটেও জাদুর কাঠি নয়। সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন রাজনৈতিক সদিচ্ছা, সাংবিধানিক সংস্কার ও জনসচেতনতা। বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিপক্বতা বিবেচনায় ধাপে ধাপে আংশিকভাবে পিআর পদ্ধতির পরীক্ষামূলক প্রয়োগ হতে পারে, যাতে করে ভবিষ্যতের জন্য একটি টেকসই ও ন্যায্য নির্বাচনী কাঠামো গড়ে তোলা যায়। ‘পিআর’ বিষয়ে একটি বহুল প্রচারিত মত, এটি পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের সরকারে যেতে সাহায্য করে। কিন্তু বেশির ভাগ গবেষণাই দেখিয়েছে, ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীগুলোর প্রতিনিধিরা খুব সামান্যই নিজ নিজ গোষ্ঠীস্বার্থ রক্ষায় নিবেদিত হয়।
পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউট ফ্রেজার ইনস্টিটিউটের মতো বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান সিদ্ধান্ত দিয়েছে পিআর পদ্ধতিকে যতটা ন্যায্য ও সাম্যবাদী মনে হয়, ততটা মোটেই নয়। বরং পৃথিবীর যে দেশেই পদ্ধতিটির প্রয়োগ রয়েছে, সে দেশেই শাসনতান্ত্রিক জটিলতা না কমে বরং বেড়েছে। হানাহানি, বিভাজন, সংকীর্ণতা, অনৈক্য ও ক্ষুদ্র স্বার্থের লড়াই বেড়েছে।
বাস্তবায়নের একাধিক উপায়
১. বদ্ধ তালিকা পদ্ধতি (Closed List PR): ভোটাররা শুধুমাত্র রাজনৈতিক দলকে ভোট দেন। দলগুলো নির্বাচনের আগে তাদের প্রার্থীদের একটি তালিকা জমা দেয়। প্রাপ্ত ভোটের আনুপাতিক হারে তালিকার ক্রম অনুযায়ী প্রার্থীরা নির্বাচিত হন।
২. মিশ্র সদস্য আনুপাতিক পদ্ধতি (Mixed-Member Proportional – MMP): এই পদ্ধতিতে কিছু আসনে সরাসরি FPTP পদ্ধতিতে এবং বাকি আসনগুলো পিআর পদ্ধতির মাধ্যমে পূরণ করা হয়। জার্মানি ও নিউজিল্যান্ডে এই মিশ্র ব্যবস্থা বেশ সফলভাবে কার্যকর রয়েছে।
৩. মুক্ত তালিকা পদ্ধতি (Open List PR): ভোটাররা দলকে ভোট দেওয়ার পাশাপাশি পছন্দের প্রার্থীকেও বেছে নিতে পারেন। দলের প্রাপ্ত আসনের সাথে প্রার্থীদের জনপ্রিয়তা বিবেচনা করে চূড়ান্ত বিজয়ী নির্ধারণ করা হয়।
বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিত
অন্তর্বর্তী সরকারের এগার মাসের মাথায় নির্বাচন পদ্ধতি নিয়ে নতুন বিতর্কে পাল্টাপাল্টি অবস্থানে বিভক্ত রাজনৈতিক দলগুলো। গণঅভ্যুত্থানে শেখ হাসিনার সরকারের পতনের পর সম্প্রতি সংবিধান সংস্কার কমিশন দ্বিকক্ষবিশিষ্ট জাতীয় সংসদ প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করেছে। যেখানে সংসদের নিম্নকক্ষে আসন থাকবে ৪০০, নির্বাচন হবে বর্তমান পদ্ধতিতে। এর মধ্যে ১০০ আসন নারীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। তারা নির্বাচিত হবেন সরাসরি ভোটে। আর উচ্চকক্ষে আসন থাকবে ১০০টি। এখানে নির্বাচন হবে সংখ্যানুপাতিক অর্থাৎ প্রপোরশনাল রিপ্রেজেন্টেশন বা পিআর পদ্ধতিতে। সংসদের দুই কক্ষ মিলিয়ে মোট আসন হবে ৫০০টি।
এই মুহূর্তে পিআর নিয়ে দলগুলোর পাল্টাপাল্টি অবস্থান আরও দৃশ্যমান হয়েছে। দেশের অন্যতম বৃহৎ রাজনৈতিক দল বিএনপি এবং এর মিত্র কিছু দল সংসদীয় আসনে সরাসরি ভোটের বিদ্যমান ব্যবস্থার পক্ষে কঠোর অবস্থান নিয়েছে। অন্যদিকে, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীসহ কয়েকটি ইসলামন্থী ও বামপন্থী দল এবং সদ্যগঠিত এনসিপিও সংসদের দুই কক্ষেই পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচনের জোর দাবি জানিয়ে আসছে।
সবশেষ, সম্প্রতি সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে জামায়াতের বৃহৎ সমাশে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব বা পিআর পদ্ধতি নিয়ে জামায়াত নেতাদের বক্তব্য নতুন করে আলোচনার সূত্রপাত করেছে। শেষ পর্যন্ত নির্বাচন পদ্ধতিকে ঘিরে তৈরি হওয়া বিতর্কই আগামী নির্বাচনকে ক্ষতিগ্রস্ত করার আভাস দিয়েছেন বিএনপি নেতারা।
বিএনপি পিআর পদ্ধতির বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান নিয়ে বলেছেন, সরকারের ঘনিষ্ঠ একটি অংশ নিজেদের স্বার্থে ‘নতুন ইস্যু’ সামনে এনে নির্বাচন পেছানোর চেষ্টা করতে পারে। তবে জামায়াত নেতারা জানান, প্রচলিত পদ্ধতিতে জনমতের প্রতিফলন ঘটছে না বলেই তারা পিআর পদ্ধতি চাইছেন।
বিশ্লেষকরা বলছেন, রাজনৈতিক সুবিধা আদায়ের জন্য সরকার কিংবা অন্য কারও ওপর চাপ তৈরির জন্যই ‘পিআর পদ্ধতিতে’ নির্বাচনের দাবিটি সামনে আনা হয়ে থাকতে পারে। তবে তারা এও মনে করেন যে, নির্বাচন পদ্ধতি নিয়ে দলগুলোর মধ্যে দূরত্ব না ঘুচলে সেটি আগামী বছরের শুরুতে অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনকে সংকটে ফেলতে পারে।